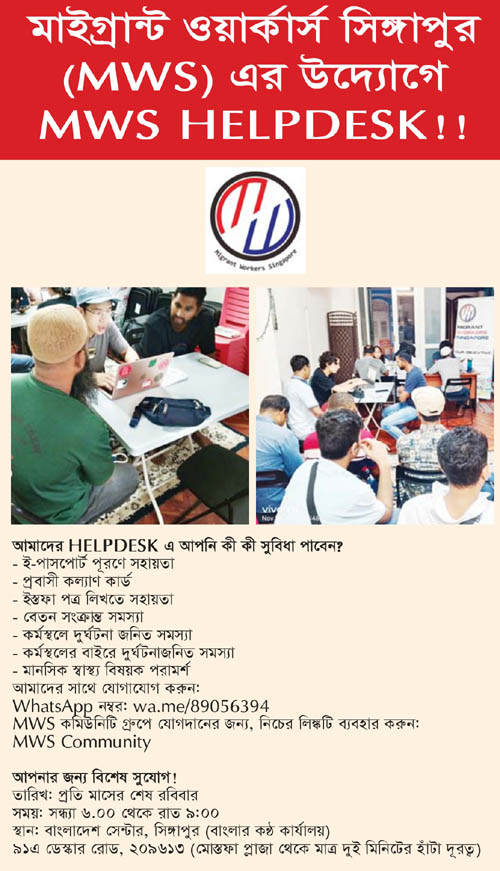সালটা সম্ভবত ১৯৬৬। আমি তখন ৮। বাবা সদ্য দেশে ফিরেছেন, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি শেষ করে। আমাদের জয় করতে ছুটির দিনে পুরোনো গিটারে ধরেন– ‘আগে জানলে, আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না... আর দূরের পাড়ি ধরতাম না।’
শুক্রবারে নিয়ে এলেন নতুন এক খেলা। ‘ঘুম থেকে ওঠো সব, আসছে পহেলা বৈশাখ’। আমাদের তো অনেক নববর্ষের কার্ড বানাতে হবে। আমাদের আজিমপুর কলোনির ২৬/এ বাসায় যেন উত্তেজনার বন্যা বইছে। পেইন্ট বক্স থেকে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রং ঈগলুর ছোট ছোট কাপে গোলালেন। নিয়ে এসো তোমাদের ফেলে দেওয়া পুরোনো দাঁতের ব্রাশ। কাগজ কেটে লিখলেন শুভ নববর্ষ। তারপর যার যার খাতার পাতা দুই ভাঁজ করে ওপরে সেই ‘শুভ নববর্ষ’ লেখাটি সেঁটে দিয়ে শেখালেন, কী করে ব্রাশ রঙে চুবিয়ে তর্জনীর টান দিয়ে রঙের ফোয়ারা বইয়ে দেওয়া যায়। অবাক কাণ্ড! শুভ নববর্ষ লেখাটা সরাতেই হয়ে গেল নববর্ষের কার্ড। সৃষ্টির সে কী উন্মাদনা! ৮ বছর বয়সে সেই আমার বাংলা নববর্ষের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয়।
প্রতিবছর বাবার সঙ্গী হই তাঁর বর্ষবরণের সাহিত্য সভাগুলোতে। ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা ধরে শুনতে হতো মোগল বাদশাহ আকবর কবে এই বর্ষবরণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন। আলোচনা শুনতে শুনতে অধৈর্য হতাম বটে, কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য রুপার কাঠি মনের মাঝে তৈরি করে দিত এক আত্মপ্রত্যয়ের চেতনা– আমার রয়েছে এক দারুণ সুন্দর ঐতিহ্যে ভরা অতীত। যে অতীত পহেলা বৈশাখে এসে বিশেষভাবে আমাদের জানান দেয় তার অস্তিত্ব।
ছেলেবেলার
ঈদ, মহররম বা পহেলা বৈশাখের
সঙ্গে মিলেমিশে ছিল মেলা। মামা
একান্নবর্তী পরিবারের ছোটদের নিয়ে যেতেন মেলাতে।
প্রথমেই হাতে চাই– মুরলী।
কেউ নিত মুড়কি অথবা
গুড়ের সাজ। ছোট বোন
রিফির চাই মাটির পুতুল।
মামাতো ভাই জামিল যখন
গামলার পানিতে মেলা থেকে আনা
লঞ্চ চালাত, চারপাশ থেকে উপুড় হয়ে
সবাই মজা নিতাম। ভোলা
কি যায় রুমি ভাইয়ের
সেই স্প্রিং গলার সাদা দাড়ির
বুড়ো? টমবয় রিমা বা
নিনির দড়িতে টানা ডুগডুগি পরবর্তী
১০ দিন সবার কান
ঝালাপালা করে দিত। ডোরাকাটা
কাগজের সাপ দিয়েই ভয়
দেখাত সোহেল ভাই। খেলার সাথি
চিকুনি নিত স্বচ্ছ লাল
কাগজের চশমা। সেই বয়সেই ঘরকন্নায়
দারুণ উৎসাহী আমার চাই হাঁড়িপাতিল।
সেবার মেলায় মাঝ রাস্তায় কারও
ধাক্কা খেয়ে আমার ফ্রকের
কোল থেকে পড়ে ভেঙে
গেল সাধের হাঁড়িকুড়ি। পথের মাঝে পা
ছড়িয়ে বসে আমার সে
কী কান্না! ‘ফিরে চলো সেই
দোকানে। আবার কিনে দাও,
প্লিজ।’ তা কি হয়?
না পাওয়ার বেদনা নিয়েই অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী
মেলার জন্য।
আজিমপুরে আমাদের সামনের বিল্ডিংয়ে থাকতেন মীনাক্ষী আপারা। তাঁর সঙ্গে আমাকে
আর রিমাকে গান শিখতে ছায়ানটে
পাঠাতেন মা। বাল্যবন্ধু জীবিনা
সঞ্চিতা, রোকাইয়া হাসিনা নীলিসহ আরও অনেকে যেতাম
একসঙ্গে। সেই সূত্র ধরেই
প্রথম জেনেছিলাম, রমনার বটমূলে গত বছর হয়েছে
দারুণ আনন্দের এক পহেলা বৈশাখ।
আর পায় কে! আমাদেরও
যেতে হবে সেখানে।
খালাতো বোন মলি আপা
আমাদের সবাইকে সাদা শাড়ি লাল
পাড় পরিয়ে নিয়ে গেলেন। সে
অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। সার বেঁধে বসে
‘এসো হে বৈশাখ, এসো
এসো’। কোনো এক
বৈশাখে কেউ একজন বলেছিল,
‘আরে সবাই বটমূল বলছে
কেন? এ তো অশ্বত্থ
গাছ!’
কৈশোর
পেরিয়ে যৌবনে যখন পা দিলাম,
নববর্ষের আরেক রূপ। দেশ
তখন স্বাধীন। এবারে কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে পহেলা বৈশাখ। রিমা আমাদের ডাটসান
ব্লু-বার্ড গাড়ি চালিয়ে, গাড়ি
ভরে সব বান্ধবীকে তুলে
রমনা পার্কে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভোরের আলো বেশ স্পষ্টই
হয়ে যেত! তাতে কী!
আর একটু পরে যখন
বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন প্রায় সব
বান্ধবীরই একটু একটু প্রেমট্রেম
হচ্ছে। রমনার মাঠ বা ধানমন্ডির
মাঠে কারও পাশে দাঁড়িয়ে
গান শোনা। সে পহেলা বৈশাখ
যেন রোমাঞ্চে টইটম্বুর। সবার সঙ্গী সময়মতো
এলেও আমাকে কিন্তু অপেক্ষা করতে হতো সকাল
১০টা পর্যন্ত। কারণ আমার প্রেমিক
পুরুষ ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। হালখাতা তাদের বড় এক আচার।
হালখাতার মিলাদ পড়ে মিষ্টির প্যাকেট
হাতে নিয়ে আবরার আসত!
মৃদু অভিমান প্রকাশও যেন আনন্দ অনুভূতি!
১৯৮০ সালে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। পহেলা বৈশাখে যাওয়া কিন্তু থামল না, বরং যুক্ত হলো আবরারের কাছ থেকে একটা তাঁতের শাড়ি পাওয়া। আর সেই শাড়ি পরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন। আমাদের জেনারেশন সাক্ষী বাংলার কৃষকের পহেলা বৈশাখের শহুরে রূপান্তরের। সম্ভবত ’৮৫-র দিকে শুরু হলো আর্ট কলেজের আনন্দ শোভাযাত্রা। হাতে আমপাতা, ডালা-কুলা, টোকা সহযোগে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়াতে ছেলেমেয়ে, ভাগনে-ভাগনিদের ছিল মহা-উৎসাহ। আশির দশকের শেষের দিকে শহুরে মধ্যবিত্তের পহেলা বৈশাখ এক নতুন জোয়ার পেল। গার্মেন্ট শ্রমিক, সেবা শ্রমিক সবার যোগদানে পহেলা বৈশাখ পরিণত হলো এক গণসংস্কৃতিতে।
হঠাৎ খেয়াল করলাম, পহেলা বৈশাখ ঘিরে কিছু বিতর্ক। আনন্দ শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন করে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ হিসেবে ইউনেস্কোতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ঘুড়ি, বাঁশি, একতারার মতো আবহমান বাংলার মোটিফগুলো প্রতিস্থাপিত হয়ে যাচ্ছে এমন কিছু মোটিফ দ্বারা, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এখানেই শেষ নয়; যুক্ত হচ্ছে শিংওয়ালা গোলাপি শাড়ির খালেদা বা রাজাকারের বিভিন্ন ট্যাগ। অর্থাৎ শোভাযাত্রাটি আর অরাজনৈতিক থাকল না। পহেলা বৈশাখের এই রাজনীতিকীকরণের উল্টো প্রতিক্রিয়াও আসতে শুরু করে রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর থেকে। শোভাযাত্রার রাজনীতিকীকরণের বয়ান সরাসরি পহেলা বৈশাখ উদযাপনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে বসে। এ দুইয়ের টানাপোড়েনে হারিয়ে যেতে থাকে পহেলা বৈশাখের মূল আদর্শ।
পহেলা বৈশাখ প্রেরণা দেয় নতুন উদ্দীপনায় আমাদের ভেতরকার সৃজনশীলতা বিকাশের; উৎসবের আনন্দ জড়িয়ে রেখে জীবনকে উপভোগ করা আর এগিয়ে চলার। এবার অন্য এক ক্রান্তিকাল! সুযোগ এসেছে পহেলা বৈশাখকে তার আদি ঐতিহ্য ফিরিয়ে দেওয়ার। পহেলা বৈশাখকে পেতে চাই বাঙালি, চাকমা, মারমা, হাজং, সাঁওতাল বা উর্দুভাষী– সবার কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। নতুনকে আলিঙ্গনে তার প্রসারতার বিচারে। আমরা আজ যেমন বাংলাদেশের, তেমনই দক্ষিণ এশীয় বা আরও পরে বিশ্ব-সংস্কৃতির অংশ। তাই এবারের পহেলা বৈশাখে খুঁজতে চাই শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, লাওস বা মিয়ানমারের পহেলা বৈশাখে দুধ আর চালের তৈরি নানা পদের খাবার কেন বড় মোটিফ? জানতে চাই উত্তর আফগানিস্তানে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে কেন ব্যবহৃত হয় গন্ধম (গম), দূর্বাঘাস আর আয়না? বুঝতে চাই বাদশাহ আকবর কি ইরান বা টার্কির, নওরোজের কোনো রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমাদের পহেলা বৈশাখ উদযাপনে? এবারে সুযোগ এসেছে এমন এক পহেলা বৈশাখের, যা আমাদের সবাইকে কাছে টানতে শেখাবে; বিভেদ শেখাবে না। ভালোবাসতে শেখাবে; ঘৃণা করতে নয়। তবেই সার্থক হবে আমার বাবা ড. আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতা– ‘আস বর্ষ, নববর্ষ, আন হর্ষ, বৃষ্টির জাদুতে আর সৃষ্টির নেশায়’।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, রামরু
You Must be Registered Or Logged in To Comment লগ ইন করুন?

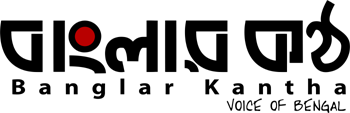

 অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী