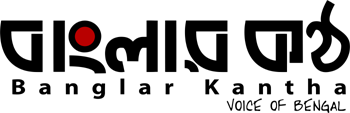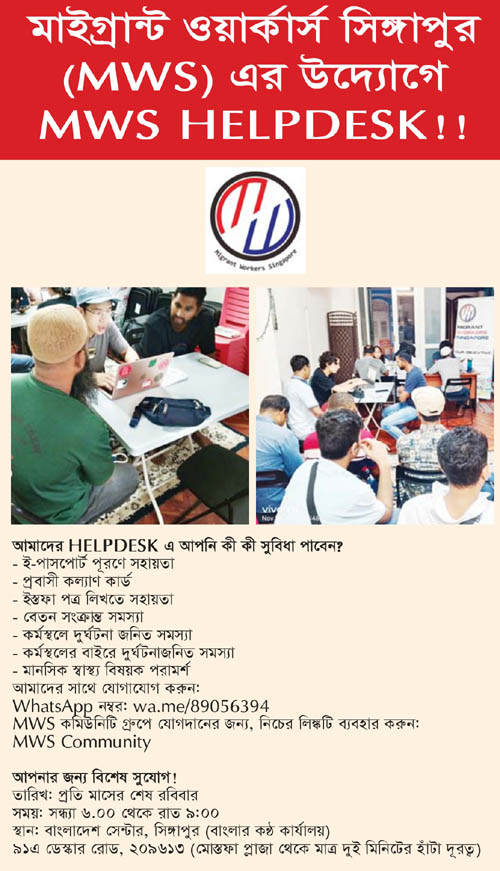সাতচল্লিশে পাকিস্তান সৃষ্টির পর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে তৎপর হয়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৪৮ সালের মার্চে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সাতচল্লিশে পাকিস্তান সৃষ্টির পর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে তৎপর হয়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৪৮ সালের মার্চে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। প্রথম প্রতিবাদ আসে তৎকালীন পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। আর এতে বড় ভূমিকা রাখেন নারী শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক কর্মীরা। রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি এর বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরির ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তারা।
জিন্নাহর ওই ভাষণের আগে থেকেই পূর্ব বাংলার নারী শিক্ষার্থীরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে এক সর্বদলীয় সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এখানকার নারীরা প্রয়োজনে তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে বলে ঘোষণা দেন ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী মাহবুবা খাতুন। মার্চের মাঝামাঝি রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে পিকেটিং করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার হন বেশ কয়েকজন নারী শিক্ষার্থী। আইনসভায় মুসলিম লীগের নারী সদস্যরা নিজ দলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ‘স্বাধীনতায়’ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়ে এ দাবি আদায়ের আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার পক্ষে এক নিবন্ধ লেখেন যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজের শিক্ষার্থী হামিদা সেলিম। ১৯৪৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে প্রতিষ্ঠিত হয় তমদ্দুন মজলিস। সে সময় সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাশেমের পরিবারের নারী সদস্যরা ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র ‘সৈনিক’ পত্রিকা প্রকাশে সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছেন তারা। ঢাকার বাইরেও প্রতিটি জেলায়ই নারীরা তখন আন্দোলনকে বেগবান করায় ভূমিকা রেখেছেন। যেমন সিলেটে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বেগম জোবেদা খাতুন, হাজেরা মাহমুদ, রোকেয়া বেগম প্রমুখ।
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের মধ্যেও অগ্রণী ছিলেন নারী ভাষাসৈনিকরা। সে সময় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার মূল কাজটি করেছিলেন রওশন আরা বাচ্চুসহ আরো কয়েকজন নারী শিক্ষার্থী। সেদিন পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেলে অনেক নারী ভাষাসৈনিক আহত হন। তাদের মধ্যে রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, বোরখা শামসুন, সুফিয়া ইব্রাহীম, সুরাইয়া ডলি ও সুরাইয়া হাকিম উল্লেখযোগ্য। এসব ভূমিকার জন্য সে সময় নারী ভাষাসৈনিকদের অনেক নির্যাতন—অত্যাচারের মধ্য দিয়েও যেতে হয়েছে। এমনকি কারাবন্দি ভাষা সৈনিকদের ওপর নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি তাদের ওপর পারিবারিক ও মানসিকভাবে নানা ধরনের চাপে ফেলেছে তৎকালীন শাসকরা। এমনকি অনেকের শিক্ষাজীবনও শেষ করে দেয়া হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা সত্ত্বেও এ নারী ভাষাসৈনিকদের নিয়ে পরে জনপরিসরে আলোচনা হয়েছে খুবই কম। অনেকটাই বিস্মৃত হয়ে পড়েছে তাদের নাম এবং সংগ্রাম ও ত্যাগের গাথাগুলো।
স্বাধীনতার পর ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যাপকতম গণ—আন্দোলনের ঘটনা ধরা হয় চব্বিশের গণ—অভ্যুত্থানকে। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া এ আন্দোলনকে গণ—অভুত্থানে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা রেখেছিলেন নারী শিক্ষার্থীরা। ভাষা আন্দোলনের মতো চব্বিশের গণ—অভ্যুত্থানেও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কম। এমনকি বায়ান্নর মতো চব্বিশের নারী আন্দোলনকারীরাও বিস্মৃতির আড়ালে হারাতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ।
গণ—অভ্যুত্থানের পরপর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারে উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের তিন প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে একজনও নারী না থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল শুরুতেই। এর পর গত ছয় মাসে জুলাই আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের ঘটনাবলি নিয়ে বিভিন্ন জনপরিসরে যত আলোচনা হয়েছে, সেখানেও নারীদের অবদানের বিষয়টি খুব কমই আলোচনায় এসেছে।
হাইকোর্টের এক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের জুনের শেষে শুরু হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন। জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে তা সারা দেশেই অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ দিনও সামনের সারিতে ছিলেন নারী শিক্ষার্থীরাই এবং প্রথমে তাদের ওপরেই হামলার ঘটনা ঘটে। আন্দোলনের পরের দিনগুলোয় সারা দেশের আন্দোলনের কেন্দ্রগুলোয় পতাকা কিংবা প্ল্যাকার্ড হাতে নারীরা সামনের সারিতে থেকে আন্দোলনে আলোড়ন তৈরি করে। রাজধানীতে আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল শাহবাগ। শাহবাগকেন্দ্রিক মিছিল ও সভাগুলোর প্রতিটিতেই সামনের সারিতে ছিলেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী শিক্ষার্থী। এমনকি বিক্ষোভ সভাগুলোয় অধিকাংশ সময় স্লোগানও দিতে দেখা গেছে নারীদের।
চব্বিশের কোটা সংস্কারবিরোধী আন্দোলনকে গণ—অভ্যুত্থানে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে আন্দোলনের গতিবেগ পাল্টে দেয়ার অনুঘটক হিসেবে কাজ করেন নারী শিক্ষার্থীরা। সেদিন রাতে হলের তালা ভেঙে প্রথম বেরিয়ে এসেছিলেন রোকেয়া হলের ছাত্রীরা। স্টিলের প্লেট, চামচ বা খুন্তি হাতে নিয়ে আওয়াজ তুলে হল থেকে বের হতে থাকেন নারী শিক্ষার্থীরা। ওই সময় নারীদের নানা রকম স্লোগানে স্লোগানে চারপাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। এর পরই একে একে অন্যান্য হলের নারী শিক্ষার্থীরা বের হয়ে রাজু ভাস্কর্যে সামনে মিলিত হন। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই সারা দেশের মানুষের কাছে পেঁৗছে যায় আন্দোলনের বার্তা। ওই রাতেই দেশের অন্য ক্যাম্পাসগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন। অধিকাংশ ক্যাম্পাসেই নারী শিক্ষার্থীরা হলের তালা ভেঙে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদে অংশ নেন।
বাংলাদেশের প্রতিটি সংগ্রামের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে নারীদের ভূমিকা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংগ্রাম শেষে অনেক কিছু গঠনের প্রশ্ন আসে, সেই কাজগুলোয় নারীরা অনুপস্থিত। এটিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়, যাতে মনে হয় নারীরা ইচ্ছা করেই আসছে না। কিন্তু এটি সঠিক নয়। বরং আমাদের এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা আদিকালের। এখানে এমনভাবে ব্যবস্থাটি চলে; বিশেষ করে রাজনীতির মাঠে, যা নারীর উঠে আসার প্রতিকূলে। উদাহরণ হিসেবে ‘ভাইয়ের রাজনীতির’ কথা বলা যায়। ‘ক্ষমতার ভাইদেরকে’ কেন্দ্র করে আবর্তিত রাজনীতিতে নারীরা স্বস্তি পান না। বরং নারীরা নিজ নিজ দায়িত্বের জায়গা থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত হন। যেখানে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করাই ওই নারীদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। কিন্তু রাজনীতির কাঠামোগত সমস্যার জন্য এটিতে ভীষণরকমভাবে ব্যাঘাত ঘটে। চব্বিশের গণ—অভ্যুত্থানের পর নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে আমরা কাজ করছি। আমাদের লক্ষ্য নারীদের যোগ্য করে তোলা। যার জন্য ট্রেনিং, সেমিনারসহ নানা রকম কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছি। যেখানে প্রয়োজন দায়িত্বের রাজনীতি, ক্ষমতার নয়।
পূর্ব বাংলার নারীরা রাজনীতিতে সক্রিয় হতে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অংশগ্রহণ ছিল তাদের। পরবর্তী সময়ে আন্দোলন—সংগ্রামগুলোয় শুধু সামনের সারিতেই নয়, আন্দোলনের নেতৃত্বের স্থানেও জায়গা করে নেয় নারীরা। ব্রিটিশ আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী লীলা নাগ, মাস্টারদা সূর্য সেনের সহযোগী কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তেভাগার নেত্রী ইলা মিত্র, হাজং বিদ্রোহের নেত্রী কুমুদিনী হাজং, রাশমনি হাজং প্রমুখ নিজ নিজ সময়ের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ।
বাংলাদেশের ইতিহাসের সব আন্দোলনেই নারীরা অংশগ্রহণ করেছে। কখনো অস্ত্র হাতে, কখনো—বা নিরস্ত্র। একাত্তরের আন্দোলনে অস্ত্রের পাশাপাশি অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়ানোসহ নানানভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাশে দাঁড়িয়েছে। জুলাই গণ—অভ্যুত্থানেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কাজের মধ্য দিয়েই তাদেরকে নিজেদের জায়গা নিজেরা তৈরি করে নিতে হবে। পুরুষরা তৈরি করে দেবে এমনটি ভাবলে চলবে না। আমাদের সমাজের নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়লেও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা, নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় এখনো নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এসব জায়গায় নারীদের নিজেদেরকেই সম্মিলিতভাবে কাজ করে আগামী দিনের জায়গাটি নির্ধারণ করতে হবে।
You Must be Registered Or Logged in To Comment লগ ইন করুন?